১৯৮৯ সালটি হল আদি শঙ্করাচার্যের ১২০০তম জন্মবর্ষ। এই জন্মবর্ষ গোটা দেশে পালিত হচ্ছে, সর্বোপরি পালন করা হচ্ছে তাঁর নিজের রাজ্যে। কেরালা সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তর এই মহান সাধুর জন্মস্থান কালাডিতে একদিনের সেমিনারের আয়োজন করছে, যেখানে কেরালার এই বিশিষ্ট সন্তানের যে শিক্ষা, তার কিছু দিক নিয়ে আলোচনা হবে।
এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল যদি মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা এই সেমিনারে যোগ দেন, তবে তাঁরা কি দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী ও কর্মীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। না, কারণ তাঁদের পক্ষে উচিত কাজ হবে না কি আদি শঙ্করাচার্যের দর্শনের বিরোধিতা করা?
ভাববাদ বনাম বস্তুবাদ
কথাটা উঠছে এই কারণে, এটা ধরেই নেওয়া হয় যে, ভাববাদ ও বস্তুবাদ একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে এবং সবসময়ে সর্বত্র তাদেরকে একে অপরের বিরোধিতা করতে হবে। সেক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করা হয় না বাস্তব জীবনের এবং মানুষের চিন্তার জগতে অন্যান্য বিপরীত প্রবণতার মতোই ভাববাদী ও বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তাধারায় যে বিপরীতমুখী প্রবণতা, তা একে অপরের সঙ্গে অধিবিদ্যামূলক সম্পর্কে যুক্ত নয়, বরং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটি দ্বান্দ্বিক। ভাববাদ অথবা বস্তুবাদ উভয়ের কেউই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই-উভয়েই এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে-সব সময়েই একে অপরকে খারিজ করছে এবং এই যে নতুন নতুন প্রকরণের মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে, সেটাই হল মানবিক চিন্তাধারা বিকাশের নিয়ম। সুতরাং একথা মনে করার কারণ নেই যে, বস্তুবাদ, ভাববাদের থেকে যেন উৎকৃষ্ট এবং ভাববাদ বস্তুবাদের থেকে যেন নিকৃষ্ট। লেনিন তাঁর ‘দার্শনিক নোট বইয়ে’ বলেছেন, “কেবলমাত্র স্কুল, সহজ, অধিবিদ্যামূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই দার্শনিক।
আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
ভাববাদকে অর্থহীন বলা হয়। অপরদিকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অবস্থান থেকে দার্শনিক ভাববাদ হল একতরফা, জ্ঞানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, দৃশ্যরূপ, বিশেষ দিক যা নিরঙ্কুশ, বস্তু ও প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, দেবত্বে মহিমান্বিত। ভাববাদ হল যাজকীয় দুর্জেয়তাবাদ। একথা সত্যি। কিন্তু দার্শনিক ভাববাদ (‘আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে’ এবং ‘সেইসঙ্গে’) হল যাজকীয় দুর্জেয়তাবাদের পথে অনন্ত জটিল জ্ঞানের (মানুষের দ্বান্দ্বিকতা) একটি অন্যতম ছায়া।।
মার্কস এবং এঙ্গেলস যেমন সর্বোৎকৃষ্ট ভাববাদী দার্শনিকের (হেগেল) শিষ্য ছিলেন, লেনিনও মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাববাদের অবদানকে বিরাট মূল্য দিতেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভাববাদ ও বস্তুবাদ পারস্পরিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে উভয়ে বিকশিত হয়েছে, নতুন নতুন কায়দায় বারে বারে একে অপরকে নাকচ করেছে, যার পরিণতিতে উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভাব ঘটেছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের। একেবারে গোড়ার দিকে মার্কস ও এঙ্গেলসের পরিচয় ছিল প্রতিভাধর তরুণ হেগেলপন্থী হিসাবে, তাঁরা হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতাকে আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন এবং সেইসঙ্গে সমকালীন বস্তুবাদের যা কিছু সেরা, তা আত্মস্থ করেছিলেন। তাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে একইসঙ্গে সেই সময়কার চালু ভাববাদ (হেগেলীয়) ও চালু বস্তুবাদকে (ফয়েরবাখীয় বস্তুবাদ) নাকচ করা হয়েছিল। লেনিনকেই এ বিষয়ে কৃতিত্ব দিতে হবে। কারণ তিনি মার্কস এঙ্গেলসের দর্শনকে আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন।
সর্বহারা বিপ্লবের দর্শন
মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের যে দ্বান্দ্বিক (এবং ঐতিহাসিক) বস্তুবাদ, তা হল বিপ্লবী প্রয়োগের দর্শন। মার্কস বলেছিলেন, “দার্শনিকরা এ জগতকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু মূল কথা হ’ল জগতের পরিবর্তন।” তবে তাঁদের যে দর্শন, তা শুধু যে কোনও বিপ্লবের দর্শন নয়, তা তৈরি হয়েছে সর্বহারা বিপ্লবের জন্য। মার্কসের তাঁর “Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right” গ্রন্থে লিখেছেন, “দর্শন যেমন বস্তুগত অস্ত্র পায় শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে, তেমনি শ্রমিকশ্রেণি তার আত্মিক (Spiritual) অস্ত্র খুঁজে পায় দর্শনের মধ্যে।”
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যেহেতু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, তাই তা অবশ্যই শঙ্করাচার্যের দর্শনের বিরোধী। কারণ তাঁর দর্শনই হল ভারতীয় ভাববাদী দর্শনের সর্বোচ্চ বিন্দু। তবে কোনো মার্কসবাদী একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে, সেই দর্শনের বিবর্তন হল ভারতীয় চিন্তাপ্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর এবং সেই সঙ্গে তা ভারতীয় সমাজের বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মার্কস এবং এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহারে দেখিয়েছেন “বস্তুগত উৎপাদন যেভাবে পাল্টায় সেই অনুপাতে বৌদ্ধিক উৎপাদনের চরিত্রও পরিবর্তিত হয়। প্রতিটি যুগের নেতৃত্বদানকারী ভাবধারা হল সেই যুগের শাসকশ্রেণির ভাবধারা।”
সুতরাং আমরা যদি আদি শঙ্করাচার্যের দর্শনের সমালোচনা করতে চাই, তবে আদি শঙ্করাচার্য ও তাঁর দর্শন একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন।
আমাদের উচিত হবে, ভারতীয় সমাজ ও চিন্তাধারার একটা সমীক্ষা করা। অন্য যেকোনো ভারতীয় দার্শনিকের মতো আদি শঙ্করাচার্য ছিলেন ভারতীয় সমাজেরই ফসল; তাঁর সমকালে যে ভারতীয় চিন্তাধারা ছিল তাকে শঙ্করাচার্য আরও বিকশিত করেছিলেন। যদিও তাঁর জন্ম কেরালায় (তাঁর জন্মস্থান কালাডি গ্রামটি বর্তমানে কেরালার এর্নাকুলাম জেলার অন্তর্গত) তিনি এক উচ্চস্তরের ভারতীয় পণ্ডিত হিসাবে সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি ভারতীয় ভাববাদী দর্শনের যা কিছু সেরা, সেগুলিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও কর্ম শুধু কেরালাকেই নয়, সারা ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছিল।
শ্রেণীসংগ্রাম
তাহলে ভারতীয় সমাজের চেহারাটা ঠিক কীরকম? এই সমাজ ও তার চিন্তাধারা কীভাবে বিকশিত হয়েছিল? মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহারে লিখেছিলেন, “বর্তমান সমাজের যে লিখিত ইতিহাস রয়েছে, তা হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।” এক্ষেত্রে ইশতেহারে যে কথা বলা হয়েছে, তা ভারত ও ইউরোপ উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্য।
কিন্তু যেভাবে ইউরোপে “স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ড কর্তা আর কারিগর” শ্রেণির মধ্যে শ্রেণিসংগ্রাম বিকশিত হয়েছিল, ভারতে তা হয়নি। ভারতীয় সমাজের যে প্রথম বিভাজন ঘটেছিল, তা হয়েছিল চারটি বর্ণের মধ্যে। প্রথম দু’টি হল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, শেষ দু’টি বৈশ্য ও শূদ্র। এর সূচনাপর্বে দেখা যায় এক শ্রেণির লোকজনের আবির্ভাব হয়েছিল, যারা হল যোদ্ধা, এ ছাড়া আরেকটি শ্রেণির মানুষ তৈরি হয়েছিল, যাদের কাজ ছিল বিভিন্ন লোকাচার সম্পন্ন করা, যা যুদ্ধে জেতার জন্য প্রয়োজন।
সুতরাং আগুয়ান আর্যদের পক্ষে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে এই দুই শ্রেণির মানুষের সাহায্য খুবই প্রয়োজন ছিল- তাই তারা নিজেদের ‘দুইবার জন্মগ্রহণ করা’ (দ্বিজ) বলে ঘোষণা করল-অর্থাৎ তারা জনগণের বাকি অংশের থেকে শ্রেষ্ঠ-পরবর্তীকালে বাকি সমাজ বৈশ্য ও শূদ্রে বিভক্ত হল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চারটি বর্ণ আরও অজস্র জাত (Caste)-এ ছোটিজাত (Sub Castc)-এ, বিভক্ত হল-যাদের মাথায় রইল ‘দুইবার জন্মগ্রহণ করা’ দ্বিজরা, বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা।
স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণই ভারতীয় সমাজে সবথেকে বেশি কর্তৃত্বের অধিকারী। সাধারণভাবে বলা যায়, তারা ছিল সমাজের বৌদ্ধিক, নান্দনিক, বৈজ্ঞানিক ও দর্শনসহ অন্যান্য আত্মিক সম্পদের স্রষ্টা-অন্যদিকে সমাজের বাকি অংশ তৈরি করল বস্তুগত সম্পদ। তাই ভারতে শোষক ও শোষিতের মধ্যে যে বিভাজন, তা সম্পন্ন হয়েছিল বৌদ্ধিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে, পারমার্থিক ও লৌকিক জগতের মধ্যে। এই দুই বিরোধী ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই হল আমাদের বৌদ্ধিক ও কায়িক পরিশ্রমভিত্তিক সামগ্রিক সমাজের ভিত্তি।
আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
দর্শনের শিকড়
ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী ও বস্তুবাদী প্রবণতা কিভাবে আবির্ভূত হয়েছিল, তা এর থেকেই বোঝা যায়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন- “কোনো দর্শনে যখন জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তার নিন্দা করা হয়, তখন বুঝতে হবে জীবন থেকে পালিয়ে গিয়েই এই দর্শনের চর্চা করা হয়েছিল। প্রাচীন গ্রিসে যেমন দাস সমাজের বিকাশ ঘটেছিল, ঠিক সেইরকম উপনিষদের যুগে ভারতে বস্তুগত জগৎকে ধিক্কার জানানো হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, এইগুলি কোনোকিছুই স্থায়ী নয়, এই সবই ছিল ‘বিশুদ্ধ যুক্তি’ এবং ‘বিশুদ্ধ জ্ঞান’-এর উপর ভিত্তি করে দার্শনিক প্রশ্নগুলি যতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া-এই ধরনের জ্ঞানচর্চা তখনই হয়, যখন সমাজের কোনো একটা অংশ সমাজের বাকি অংশের তৈরি করা উদ্বৃত্ত সম্পদের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, প্রত্যক্ষ কায়িক শ্রমের দায়িত্ব থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয় এবং যার ফলে বস্তুগত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অথচ একমাত্র শ্রমপ্রক্রিয়াই পারে চেতনা সম্পর্কিত তত্ত্বর উপরে বস্তুগত সংঘাত তৈরি করতে। যে তত্ত্ব প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন তা হয়ে দাঁড়ায় “বিশুদ্ধ তত্ত্ব’, এর ফলে চিন্তা প্রক্রিয়াটা হয়ে দাঁড়ায় নিছকই কতকগুলি ধারণা এবং যিনি বিষয়ী, তিনি জ্ঞাত অথবা বস্তু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চান এবং বস্তুজগৎকে মনে করেন অজ্ঞান। অথবা অবিদ্যার সমান।
আদিশঙ্করাচার্য ও তাঁর অদ্বৈত বেদান্তের যে দর্শন, তা হল এই ভারতীয় ভাববাদী দর্শনের সবথেকে সুক্ষ্ম ও সবথেকে পরিশীলিত দর্শন। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মকে এমনভাবে বিকশিত করেছিলেন, যা থেকে মনে হবে তিনি এমনকি ঈশ্বরকেই অস্বীকার করেছেন (ব্রহ্ম ছাড়া আর সবকিছুই অস্বীকার করেছেন); যে কারণে তাঁর বিরোধিরা তাঁকে ছদ্মবেশী বৌদ্ধ (প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ) বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। উপরোক্ত এই উপাধিটিই দেখিয়ে দেয় যে, ভারতীয় দর্শনে বুদ্ধের শিক্ষা ও ব্রাহ্মণ্য কর্তৃত্বের মধ্যে, ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে সংঘাত কতটা তিক্ততার পর্যায় চলে গিয়েছিল। যদিও শঙ্করাচার্য ঔপনিষদিক ভাববাদের হয়ে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও সফল লড়াই চালিয়েছিলেন, তবু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, তিনি বৌদ্ধ ধর্মের মতো দার্শনিক প্রবণতার সঙ্গে আপোস করেছিলেন, এই ধর্মই ব্রাহ্মণ্যবাদকে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলেছিল। তবে শঙ্করাচার্য আজও শ্রদ্ধার আসনে রয়েছেন তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য, যার সাহায্যে তিনি বৌদ্ধ দার্শনিক প্রবণতাকে পরাস্ত করেছিলেন।
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতের ভাববাদী দর্শনের শিকড় সন্ধান করেছিলেন এবং তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন কীভাবে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল। তাঁর সুপরিচিত প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান গবেষণা গ্রন্থে তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন প্রাচীন ভারতের ঔষধ বিষয়ক ধ্রুপদী গ্রন্থ চরক সংহিতা সুশ্রুত সংহিতাকে। ওই দুই গ্রন্থের লেখক সেই যুগে মানুষের দেহের সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল শরীরের অসুখ নির্ণয় করা ও তার নিরাময় করা। কিন্তু সেখানে মনুষ্য জীবনের এই বস্তুগত দিকটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা কোথাও কোনোভাবে আত্মার প্রসঙ্গ।
আদি শঙ্করাচার্য ও তাঁর দর্শন একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন টেনে আনেননি। তবে তাঁদের সে যুগে সবথেকে কর্তৃত্বকারী মতাদর্শের কাছে তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করতে হয়। তাঁরা ঈশ্বরের কাছে তাঁদের আনুগত্য জানিয়েছিলেন (অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করার জন্য এটাও ছিল চিকিৎসার অঙ্গ)।
বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ
অন্যান্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। যেসব কারিগররা ও অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী মানুষেরা কোন না কোনও কাজের ক্ষেত্রে দক্ষ ছিল, তারা যখন হাতে-কলমে কাজ করত, তখন কাজের সমস্যা সমাধানে তাদের বস্তুবাদীদের মতই চলতে হত। কিন্তু যখনই তারা সামাজিক জীবনের সাধারণ সমস্যার মুখোমুখি হত, তখনই তখনকার কর্তৃত্বকারী মতাদর্শের অর্থাৎ সেই পুনর্জন্ম, আত্মা, মোক্ষ ইত্যাদির সেবায় লেগে যেতে হত। ওষুধ তৈরি ইত্যাদি পেশাগত ক্ষেত্র থেকে দর্শনের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট বস্তুবাদী দার্শনিক প্রবণতার উদ্ভব ঘটে। যারা এই দর্শন অনুসরণ করত, তারা তাদের শিল্প বা পেশার সমস্যা ব্যাখ্যা করতে বস্তুবাদী অবস্থানই নিতে হতে। কিন্তু তখনকার শাসকশ্রেণির যে শ্রেণি-বর্ণ-জাতপাতের ভাববাদী মতাদর্শ, তার কাছেই তাদের আত্মসমর্পণ করতে হত।
একই কথা সত্য ন্যায়-বৈশেষিকদের মতো বস্তুবাদী দার্শনিকদের ক্ষেত্রেও, যাদের সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন “বস্তুবাদের অনেকটাই কাছাকাছি” কিন্তু তারাও তৎকালীন “ধর্মগ্রন্থের কর্তৃত্বকে পুরোপুরি স্বীকার করেছিল এবং আত্মা ও পুনর্জন্মের হয়ে দীর্ঘ যুক্তিবিস্তার করেছিল।” তবে দেবীপ্রসাদ এই কথাও বলেছেন, “ন্যায়-বৈশেষিকদের গ্রন্থগুলিতে অত্যন্ত চতুরতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, ওইসব কথাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।”
তবে এ ছাড়াও আরও কিছু বস্তুবাদী দর্শন ছিল যেমন চার্বাক এবং লোকায়তরা-যারা শাসকশ্রেণির মতাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। ভাববাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা কোনও কথা বলতে পিছিয়ে আসেনি। তাদের লেখার যৎসামান্যই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। বিরোধীপক্ষ তাদের বক্তব্যকে খণ্ডন (পূর্বপক্ষ) করার জন্য প্রতিপক্ষের যেটুকু উল্লেখ করত, তা থেকেই প্রাচীন ভারতের বস্তুবাদী চিন্তার ব্যাপকতা সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায়।
বিজ্ঞান বনাম রাজনীতি
এই দুই দার্শনিক ঘরানার মধ্যে যে বিতর্ক, তা এতই তিক্ত ও দীর্ঘমেয়াদি ছিল যে, তার পরিণতি কী হবে তা ঠিক করত ‘রাজনীতি’। কথাটা বলেছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এ কথার অর্থ কী, তা নিচের অংশটি পড়লে বোঝা যাবে।
সনাতনী ভারতীয় রাজনীতির প্রবক্তা ছিলেন আইন প্রণেতারা, তাঁদের লেখাকেই সাধারণত ধর্মশাস্ত্র বলা হত। এইসব আইন প্রণেতাদের প্রধান মাথাব্যথা ছিল সমাজ কাঠামোর নিরাপত্তা রক্ষা করা, যা তাঁদের দৃষ্টিতে ছিল আদর্শ। এই সমাজ কাঠামো চলত।
আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
বর্ণাশ্রমের নামে, যার অর্থ হল এমন এক সমাজ, যেখানে প্রতিটি মানুষের আচার-আচরণ ঠিক করবে জাত, যে জাতে সে জন্মগ্রহণ করেছে এবং জীবনের কোন পর্বে সে রয়েছে, এটাই সবকিছু ঠিক করে দেবে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে সমাজের সংখ্যালঘু অংশ, যাদের মধ্যে ছিল অভিজাতরা, পুরোহিতরা ও ব্যবসায়ীরা, তারাই সব ধরনের বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা পেতো, যদিও সেই পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু তারতম্য ছিল, সেই সময় এটাই হয়ে দাড়িয়েছিল সমাজের নিয়ম। সমাজের বাকি অংশের মানুষ, যারা ছিল প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদন থেকেই একমাত্র দ্বিজদের জন্য বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা উৎপন্ন হত, সেই বিপুল অংশের জনসাধারণকে শূদ্র বলে চিহ্নিত করে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তখনকার আইন প্রণেতারা একথাই বলতেন যে, এই প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের কেবলমাত্র বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম প্রয়োজন ছাড়া আর কোনো কিছু ভোগ করার তাদের কোনো অধিকার নেই। তাদের একমাত্র কর্তব্য হল, সমাজের ওপরের অংশকে সেবা করা, কারণ স্রষ্টা ঈশ্বর সুনির্দিষ্টভাবে তাদের এই কাজ করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন।
ভারতে ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে যে সংগ্রাম, তা ঘুরিয়ে বলতে গেলে ভারতীয় ধাঁচের শ্রেণিসংগ্রামেরই একটি প্রকাশ- যার একদিকে সংখ্যালঘু উচ্চবর্ণের দ্বিজরা এবং অপরদিকে বিপুল অংশের সাধারণ মানুষ। এই দ্বিতীয় অংশ, যারা তাদের বেঁচে থাকার জন্য কায়িক শ্রম করত, তারা কাজের সূত্রেই প্রকৃতির নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিয়ত সংস্পর্শে থাকত। স্বাভাবিকভাবেই জগৎ সম্পর্কে যে ধারণা তারা তৈরি করেছিল, তা ছিল বস্তুবাদী। অপরদিকে সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় মানুষজন সারাক্ষণ যৌদ্ধিক কাজকর্ম করত, তাদের কাজের ধর্ম ছিল মানসিক ক্ষেত্রে, প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল না। তারাই ক্রমে ক্রমে ভাববাদীতে পরিণত হল এবং বলতে শুরু করল যে প্রকৃতির উপরে ভাবজগতের আধিপত্য রয়েছে। এই ভাববাদী দর্শনের সবথেকে পরিশিলীত প্রকাশ দেখা গেছে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবেদান্তের দর্শনে, যেখানে বলা হয়েছে ব্রহ্ম ছাড়া সবই অবিদ্যা, অর্থাৎ অস্তিত্বহীন।
কারিগর ও অন্যান্য যে অংশের মানুষ গায়ে-গতরে শ্রম করত, সেই বিপুল অংশের সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই নানা ঘরানার বস্তুবাদ উঠে আসে। তবে সামগ্রিকভাবে এই শ্রেণি এবং তাদের মতাদর্শের প্রতিনিধিরা সম্পূর্ণতই ভাববাদী দার্শনিকদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল। বৌদ্ধ এবং বৈদান্তিকদের মধ্যে যে চূড়ান্ত লড়াই হয়েছিল, তার অন্তিম পর্বের লড়াইয়ে ভাববাদী শিবিরের সর্বাধিনায়ক ছিলেন শঙ্করাচার্য। বৌদ্ধ বস্তুবাদীদের পরাজয়ের অর্থ ছিল, কর্তৃত্বকারী উচ্চবর্ণের জয়, যাদের তাত্ত্বিকরা ভাববাদকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন।
বিজ্ঞান: বিকাশ ও অধঃপতন
এই দুই মতাদর্শগত প্রবণতার মধ্যে যে লড়াই, তাতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল। প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান এতই উন্নত ছিল যে, প্রাচীন সভ্যতা ও বিজ্ঞানের নিরিখে এই দেশ অন্য দেশের তুলনায় শুধু সমকক্ষই ছিল না, বহু দেশের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত।
আদি শঙ্করাচার্য ও তাঁর দর্শন একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন ছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্যের হাতে বৌদ্ধ বস্তুবাদীদের পরাজয়ের ফলে ভারতীয় বিজ্ঞানের বিকাশ বড় রকমের ধাক্কা খায়। ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রদূত ঐতিহাসিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখছেন; শঙ্কর যেভাবে বেদান্ত দর্শনকে সংশোধিত ও প্রসারিত করলেন এবং যার মধ্যে দিয়ে এ কথাই শেখানো হল যে, এই বস্তুগত জগৎ হল মিথ্যা, এর ফলে ভৌতবিজ্ঞানের চর্চা সমাজে তার সম্মান হারাল। কণাদ ও তার ব্যবস্থাকে নির্দয়ভাবে সমালোচনা করেছিলেন শঙ্কর।
বেদান্ত সূত্রের উপর শঙ্করের যে ভাষ্য, তার থেকেই দু’একটা উদ্ধৃতি করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। যেমন শঙ্কর বলছেন, “এখানে যে পরমাণু তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, তার যুক্তি অতি-দুর্বল এরা একথা মানে না যে, ঈশ্বরই জগৎ। কারণ ধর্মশাস্ত্রেই একথা আছে, তারা মনু ও অন্যান্য কর্তৃত্বকেও মানে না। তাই যেকোনো উচ্চচিন্তাসম্পন্ন মানুষ, যাঁরা নিজেদের আত্মিক উন্নতি ঘটাতে চান, তাঁরা এদের সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।” পরে অন্যত্র লিখেছেন, “কেন আমরা বৈশেষিকদের তত্ত্বকে গ্রহণ করতে পারলাম না, তার উপরেই আলোচনা করা হয়েছে। এই তত্ত্বকে অনেকটাই ধ্বংসাত্মক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।”
আদি শঙ্করাচার্য থেকে উপরোক্ত উদ্ধৃতি দেবার পর রায় বলেন, “যেসব জনসাধারণ জাতপাতের দ্বারা জর্জরিত, কর্তৃপক্ষর দ্বারা শোষিত এবং বেদ-পুরাণ-স্মৃতির নিষেধাজ্ঞার ঠেলায় যাদের বুদ্ধি আড়ষ্ট ও অবশ হয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে কোন বয়েলের মত বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হওয়া সম্ভব ছিল না, যিনি পথ দেখানোর মতো সুনির্দিষ্ট-আদর্শ তৈরি করে দেবেন।”
বিশ্ব ইতিহাসে ইউরোপীয় রেনেসাঁ যেখানে ভাববাদীদের কাছে বস্তুবাদীদের পরাজয়ের পর ভারত এক বদ্ধাবস্থায় আটকে গেল, সেখানে ইউরোপ মৌলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন হতে লাগল, অথচ এই ইউরোপ প্রাচীন যুগে ভারতের থেকে পিছিয়ে ছিল। বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জে ডি বার্নাল লিখেছিলেন যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁ “অভিজাতদের তত্ত্ব ও জনসাধারণের প্রয়োগ এই উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তাতে কিছুটা প্রলেপ দিয়েছিল। বার্নাল আরও লিখেছেন (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর গ্রন্থে ১০১-১০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন) “যেটা প্রকৃতই নতুন, তা হল সুতো তৈরি, বস্ত্রবয়ন, বাসন তৈরি, কাঁচ তৈরি প্রভৃতি হাতেকলমে কাজের যে শিল্পী এবং সর্বোপরি খনি ও ধাতু শ্রমিকরা, যাঁরা সম্পদ ও যুদ্ধের চাহিদা মেটাত, তাঁদের মর্যাদা দেওয়া শুরু হল। শিল্পকলায় যে কৃৎকৌশল, তা রেনেসা যুগেরই বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন যুগের নয়- তার কারণ এই কৃৎকৌশল ক্রীতদাসদের হাতে ছিল না, ছিল স্বাধীন মানুষদের হাতে- মধ্যযুগে এইসব কৃৎকৌশল নতুন সমাজের শাসকদের থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনেক দূরে ছিল। রেনেসাঁ যুগে যে কারুশিল্পীদের মর্যাদা বাড়ল, তাতে তাদের যে ঐঐতিহ্য, তার সঙ্গে পণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে যে বিভেদ ঘটেছিল একেবারে সূচনা পর্বে, সেই বিচ্ছেদের অবসান ঘটিয়ে সম্পর্কের নবীকরণ ঘটল।
আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
রাজনৈতিক পরিণতি
বিষয়টি শুধু ভারত ইতিহাসে বিজ্ঞানের অধঃপতনের প্রশ্ন নয়। এটি হল সেই বিষয়, যাকে কার্ল মার্স বলেছেন, প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের, “অমর্যাদাকর, বদ্ধদশাপ্রাপ্ত, উদ্ভিদসুলভ নিশ্চল জীবন,” মার্কস দেখেছিলেন যে ভারতে গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলি ‘জাতপাত ও ক্রীতদাসত্বের দ্বারা কলুষিত।” মার্কস আরও দেখেছিলেন “প্রকৃতির এমন পূজা যা মানুষকে পশু করে তোলে, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমান অর্থাৎ বানর শবলাদেবী রূপী গোরুর অর্চণায় নতজানু করে অধঃপতনের পরিচয় দিয়েছে।”
এর একটি রাজনৈতিক ফলাফলও ছিল, তা এই যে, ভারত তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। মার্কস লিখছেন, “মোঘলদের একচ্ছত্র ক্ষমতাকে ভেঙেছিল মোঘল শাসনকর্তারা। শাসনকর্তাদের ক্ষমতাকে চূর্ণ করল মারাঠারা। মারাঠাদের ক্ষমতা ভাঙল আফগানরা এবং সবাই যখন সকলের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত, তখন দ্রুত প্রবেশ করল ব্রিটেন এবং সকলকেই পদানত করতে সক্ষম হল।”
মার্কস বলছেন, এ ঘটনা ঘটল এমন একটা দেশে, “যার কাছ থেকে আমরা (ইউরোপীয়রা) ভাষা শিখেছি, ধর্ম শিখেছি।’ স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কেন এবং কী কারণে আমাদের দেশ সেই এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত থেকে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে অধঃপতনে এসে পৌঁছাল? এর উত্তর এই যে, শোষিত জাতগুলি ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের কাছে পরাস্ত হয়েছিল এবং জয়ী হয়েছিল প্রভুত্বকারী উচ্চবর্ণগুলি, যাদের তাত্ত্বিকরা ভাববাদকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন।
ইউরোপ ও ভারত: তুলনা
শঙ্করাচার্যের দর্শনের বিবর্তন ও তার সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করার পর এখন আমি আলোচনা করতে চাই বর্তমান বিশ্বে, বিশেষ করে ভারতে ওই দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা। শঙ্করাচার্য এমন একটা সময়ে জীবিত ছিলেন এবং তাঁর কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত ছিলেন, যখন গোটা বিশ্বজুড়ে ভাববাদী ও বস্তুবাদীদের মধ্যে তীব্র লড়াই চলছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এক্ষেত্রে একটা বড় পার্থক্য ছিল ইউরোপে যে লড়াই হয়েছিল, তাতে কোন একপক্ষ চূড়ান্ত জয়লাভ করেনি; দুই ঘরানাই তাদের সংঘাত নিয়েই সমান্তরালভাবে চলেছিল, ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল। যারই পরিণতিতে উনবিংশ শতাব্দীতে দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল। যার একদিকে হেগেল, অন্যদিকে ফয়েরবাখ। বিশ্ব ইতিহাসে এই প্রথম মার্কস ও এঙ্গেলস নতুন ঘরানার দর্শন হাজির করলেন, যে ঘরানায় হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বকে ও ফয়েরাখের বস্তুবাদকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, আবার হেগেলীয় ভাববাদ ও ফয়েরবাখের অধিবিদ্যাকে বাতিল করা হল। যে দ্বন্দ্বমূলক ঐঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব উঠে এল, যার প্রবক্তা মার্কস ও এঙ্গেলস, সেই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বের দর্শন নতুন এক স্তরে উন্নীত হল।
আদি শঙ্করাচার্য ও তাঁর দর্শন একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন
কিন্তু ভারতে দুই দার্শনিক প্রবণতার মধ্যে লড়াইয়ে একপক্ষের (বস্তুবাদীদের) পরাজয় ঘটল এবং অপরপক্ষের আধিপতা বাড়ল। তবে এই লড়াই ছিল অসম, কারণ সেই সময়কার সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (জাতপাতের সমন্বয়ে তৈরি শাসন ব্যবস্থা) পুরোদস্তুর ভাববাদীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে বস্তুবাদের বিরোধিতা করেছিল। আমাদের দেশে এই যে একপক্ষ জয়ী হল, অপরপক্ষ পরাজিত হল এ শুধু দুই বিমূর্ত দর্শনের মধ্যে লড়াই ছিল না, বরং দুই সামাজিক শ্রেণি-একপক্ষ প্রভুত্বকারী, অপরপক্ষ শোষিত-উভয়পক্ষই তাদের দর্শনকে তাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল। তাই শঙ্করাচার্য ও তাঁর দর্শনের জয়লাভ ছিল ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য প্রভুত্বকারী জাতগুলির জয় এবং ভারতীয় সমাজের বাকি অংশের পরাজয়।
ভাববাদ সম্পর্কে মার্কসবাদীদের আচরণ কীরকম হবে
সুতরাং আজকের ভারতে, আজকের বিশ্বে শঙ্করাচার্যের দর্শনকে প্রাসঙ্গিক বলে কোনও চিন্তাশীল মানুষ মনে করবেন এটা চিন্তা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আরও অন্যান্য ভাববাদী দর্শনের মতো এই দর্শনেরও সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধিতা করতে হবে, যদি আমাদের দেশ ও সামগ্রিকভাবে মানবতাকে বর্তমানে দুনিয়া-কাঁপানো অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হয়। বিশেষ করে যদি একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ নতুন ভারত গড়তে হয়, তবে তার আবশ্যিক পূর্ব-শর্ত হল হিন্দু পুনরুত্থানবাদ এবং বৈদিক ও উপনিষদের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করার বিরুদ্ধে লড়াই করা।
এই প্রসঙ্গে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই আরএসএস’র মতো ‘সামাজিক-সাংস্কৃতিক’ সংগঠন, বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি যেভাবে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রচার ও প্রয়োগ করছে, তাতে আমাদের জাতীয় ঐক্যের পথে প্রভৃত ক্ষতি হচ্ছে। বর্তমানে যে রাম জন্মভূমি আন্দোলন হচ্ছে, এই ধরনের আন্দোলনগুলি আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক অথচ এইগুলিই হল আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্য ও অংশ। এইসব আন্দোলনের সংগঠকরা বৈদিক ও উপনিষদের ঋষি ও তাঁদের উত্তরসূরি শঙ্করের নাম গ্রহণ করে নিজেদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় ঐক্যের বিরোধী এইসব বিপজ্জনক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা হল বাম, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে সবথেকে বড় রাজনৈতিক দায়িত্ব।
অবশ্য এই কাজ করতে গিয়ে আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা কখনই ভাববাদী ঘরানা সম্পর্কে নিহিলিস্টাদের মতো আচরণ করব না, এই ভাববাদী ঘরানারই সব থেকে উজ্জ্বল প্রতিনিধি ছিলেন শঙ্করাচার্য। ভারতে এবং বিদেশে বহু মার্কসবাদী পণ্ডিত এই ভুল করেছেন। এক সোভিয়েত পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন কিছু মার্কসবাদী পণ্ডিত “কখনও কখনও বস্তুবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েও অবস্তুবাদী আদর্শের দ্বারা চালিত হন, যেমন তাঁদের মধ্যে এক ধরনের ব্রাহ্মণ বিরোধী মানসিকতা এবং “মুক্তি”র ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করার প্রবণতা দেখা যায়… লোকায়ত ঘরানাকে জোর করে সামনে আনা হয় এবং অপরদিকে।
আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
বেদান্ত ঘরানাকে তাঁদের তালিকায় সপ্তম এবং সর্বশেষ স্থানে জায়গা দেয়।’
ওই লেখক মনে করেন “অতীতে এবং আজও ভারতে সবথেকে প্রভাবশালী দার্শনিক ঘরানা হল বেদান্ত” এবং ‘ভারতীয় দর্শনে শঙ্করের স্থান পশ্চিমী দর্শনে প্লেটোর দর্শনের মতই উচ্চস্থানে রয়েছে।”
এবার লেখার উপসংহারে আসি। শঙ্করাচার্য ছিলেন ভারতের (এবং বিশ্বের) অন্যতম উচ্চমাপের ভাববাদী দার্শনিক, মানবজাতির জ্ঞানসম্পদে যে অবদান, তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী হল শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত। সেইসঙ্গে ভারত আরও অনেক দার্শনিকের জন্ম দিয়েছে, তাঁদের অনেকেরই চিন্তার মধ্যে বস্তুবাদের উপাদান ছিল, তার মধ্যে উল্লেখ্য ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসা, লোকায়ত প্রভৃতি, এরই সঙ্গে বুদ্ধের কথা না বললেই নয়, কারণ তিনি তাঁর প্রায় বস্তুবাদী দর্শন দিয়ে শোষিত জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছিলেন। আমরা গর্বিত এই কারণে যে, ভারতীয় দর্শনের এই উভয় ধারাই বৌদ্ধিক মহাপ্রতিভার জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু যারা বস্তুবাদী ঘরানার, তাদের লড়তে হয়েছিল এক অসম যুদ্ধ, তাই তারা পরাস্ত হয়েছিল। আরও দুর্ভাগ্যজনক, এই অসমযুদ্ধে বস্তুবাদীদের পরাজয়ের ফলে বৌদ্ধিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার সূচনা হয়েছিল, যা চলেছিল হাজার বছর ধরে এবং তারই পরিণতিতে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের পত্তন হয়।
তবে আমি আদৌ হতাশ নই। এই সর্বব্যাপক পশ্চাৎপদ অন্ধকার যুগের ধীরে ধীরে অবসান হচ্ছে। যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি খেটে-খাওয়া জনসাধারণকে দাবিয়ে রেখেছিল, তাদের বিরুদ্ধে বড়রকম আঘাত শুরু হয়েছে, যে বিদেশি শাসকরা আমাদের প্রাচীনত্বকে ধ্বংস করার কাজ করেছিল, তারা এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে; গণতান্ত্রিক শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে সামরিকবাহিনীর মতো স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে; ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।
এইসব অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণি গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকায় ধীরে ধীরে সংহত হচ্ছে; স্বাভাবিকভাবেই দ্বান্দিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ রাজনৈতিকভাবে সচেতন ভারতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের নেতৃত্বদানকারী মতাদর্শে পরিণত হচ্ছে। এটা সত্যিই এক পরিস্থিতি, যা মার্কস দেড়শো বছর আগে বলেছিলেন “দর্শন তার বস্তুগত শক্তি পায় শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে, শ্রমিকশ্রেণি তার আত্মিক অস্ত্র পায় দর্শনের মধ্যে।” নোট: 1. V.I. Lenin, Collected Works VOL 38 P 363.
2. Debiprasad Chattopadhyay, Indian Philosophy A popular introduction, People’s
publishing House, 1986, pp 85-86. 3. Debiprasad Chattopadhyay, In defence of Materlialism in Ancient
আদি শঙ্করাচার্য ও তাঁর দর্শন একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন
5. Quoted by Chattopadhyay. In defence of Materlialism in Ancient India, pp 103-04.
6. Ibid
7. Social Sciences in the USSR, No. 1, 1989, p 19(a).
সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট পত্রিকার খণ্ড-১৭, সংখ্যা ১-২, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরাজি নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ: অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
India, Peoples Publishing House, 1989, pp 16-17. 4. Ibid, pp 17-18
ধর্মনিরপেক্ষতা কী ধর্মবিরোধী?
বেশিরভাগ বিধায়ক, সাংসদ এবং মন্ত্রীরা ঈশ্বরের নামে শপথ নেন এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ ‘গভীর আন্তরিকতা’র সঙ্গে শপথ গ্রহণ করেন। এখানে ধর্মকে অস্বীকার করার কোনও ব্যাপার নেই, বরং ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং ধর্ম মানেন না, এমন মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা রক্ষা করা হয়েছে।
ধর্মনিরপেক্ষতা কী ধর্মবিরোধী?
ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে এক বিতর্কে কেরালার অর্থোডক্স খ্রিস্টান চার্চের সম্মানীয় নেতা পওলোজ মার গেগোরিয়স স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে অস্বীকার করে। একজন একনিষ্ঠ খ্রিস্টান হিসাবে তিনি সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করার কথা ভাবতে পারেন না।
তবে তিনি একথাও বলেছেন, তিনি ধর্মকে রাষ্ট্রের মদত দেওয়া অথবা কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র অবস্থান নিক-এটাও তিনি চান না। তাঁর দর্শনের ভিত্তি হল, সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা। তাই আরও এক কদম এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের উচিত নয় কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভরতুকি দেওয়া অথবা মদত জোগানো।
ধর্মপ্রাণ মানুষকে তাদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের মতো করে কাজ করতে দিতে হবে। তাঁর নিজের চার্চ ও অন্যান্য চার্চগুলির অধীনে এবং অখ্রিস্টান অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণে থাকা মানুষজনকে কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে ব্যবহার করার তিনি বিরোধী।
এক্ষেত্রে যখন প্রশ্ন ওঠে, তাঁর এই অবস্থান কী ধর্মনিরপেক্ষ নয়? তার জবাবে তিনি বলেন, না, নয়। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্মকে অস্বীকার করা।
কেরালার অর্থোডক্স চার্চের সম্মানীয় নেতার এই মূল্যায়ন ভারতীয় সংবিধানেরও। বিরোধী, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার এই উদাহরণকে তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যখন কোনো সাংসদ, বিধায়ক বা মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন, তখন ভারতীয় সংবিধানে ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের জন্য ‘ঈশ্বরের নামে শপথ’ নেওয়ার এবং ধর্ম বিশ্বাস করেন না-এমন মানুষের জন্য সংবিধানের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে “গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে শপথ” নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে এই রীতির মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করে সকল ধর্ম সম্প্রদায় এবং ধর্ম মানে না-এমন মানুষ-সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাঁদের দিক থেকে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাঁরা যেকোনো ধর্মকে রাজনৈতিক কাজে (নির্বাচন ও অন্যত্র) ব্যবহার করার বিরোধী, কিন্তু তাঁরা জনসাধারণের ধর্মীয় ভাবাবেগকে সম্মান করেন এবং তাঁরা এমন কিছু করবেন না, যা তাঁদের ভাবাবেগে আঘাত করে। তাঁরা তাঁদের ধর্ম না মানার অধিকারকে যেমন দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন, তেমনি ধর্মীয় মানুষজনের নিজস্ব ধর্মে বিশ্বাস ও পালনের অধিকারকে সম্মান করেন। ঘুরিয়ে বলতে গেলে তাঁরা ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে তাঁদের নিজ ক্ষেত্রে যা প্রাপ্য, তা দেওয়ার পক্ষপাতী “ঈশ্বরকে যা দেওয়ার তা ঈশ্বরকে দাও, রাষ্ট্রকে যা দেওয়ার, তা রাষ্ট্রকে।” ধর্মনিরপেক্ষতার এই বাক্য এবং আদর্শকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বিশ্বাস করে।
যদিও আরও কিছুটা এগিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদীরা শোষক শ্রেণি যে ‘ধর্ম’কে বিশ্বাস করে এবং পালন করে, তার বিরুদ্ধে প্রকৃত ধর্মের যা কিছু ইতিবাচক খুঁজে বের করে। মধ্যযুগে ইউরোপ এবং এশিয়াতে যে ধর্মীয় রাষ্ট্র ছিল, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তার বিরোধী। এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিকাশমান পুঁজিবাদ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্তর্থাত করেছিল। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে এই উত্তরণের পথে ধর্মের বিরুদ্ধেই ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল।
যাঁরা এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা ধর্মকেই আক্রমণ করেছিলেন, সামন্ত্রতন্ত্র-বুর্জোয়া শাসকশ্রেণিকে তাদের নিজস্ব স্বার্থে ধর্মকে অপব্যবহার করতে দেয়নি। এই ছিল ইউরোপের বুর্জোয়া ধর্মনিরপেক্ষতার চেহারা, যার সঙ্গে সম্মানীয় খ্রিস্টান নেতা পরিচিত। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলসের এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, ছিল না লেনিন ও ফিদেল শ্লোসহ অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদেরও। মার্কস তাঁর এক বিখ্যাত রচনায় বলেছেন যে, সাধারণভাবে সমাজের সমালোচনার সূচনাই হচ্ছে ধর্মের সমালোচনা দিয়ে।
একদম গোড়ার যুগের খ্রিস্টধর্মের আদর্শ সম্পর্কে খুবই প্রশংসা করেছেন এঙ্গেলস এবং তিনি বলেছেন, আজকের দিনের আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের দলিলের মধ্যে সেই আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাবে।
লেনিন তাঁর দিক থেকে সমস্ত ধর্মীয় ও ধর্মে অবিশ্বাসী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আলান জানিয়েছিলেন, ‘অন্য পৃথিবীতে স্বর্গ আছে কি নেই-এই নিয়ে অনুমান না করে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনার’ জন্য।
ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন, কীভাবে শৈশবে ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম তাঁকে একজন আধুনিক গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ এবং শ্রমিকশ্রেণির যোলা হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।
আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
সুতরাং এখানে আলোচ্য বিষয় হল, মূল ধর্মগুরুরা ধর্ম নিয়ে কী ভেবেছিলেন এবং পরবর্তীকালের শোষকশ্রেণির প্রজন্ম কীভাবে ধর্মকে ব্যবহার করেছে সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রাখতে ও অত্যাচার চালাতে।
লক্ষ্যণীয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ সময়ে যিনি ছিলেন সর্বোচ্চ নেতা, সেই মহাত্মা গান্ধি ভারতের গরিব মানুষকে ‘দরিদ্র নারায়ণ’ বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক গভীর ধর্মবিশ্বাসী মানুষ এবং এদেশের শ্রমিক ও কৃষকদের জীবন্ত দেবতা বলেই গণ্য করতেন এবং তাদের সেবায় জীবনভর পরিশ্রম করে গেছেন।
একজন হিন্দু মতান্ধ ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করেছিল, কারণ একনিষ্ঠ হিন্দু হয়েও মুসলিমদের প্রতি ‘গান্ধিজির সমান শ্রদ্ধা ছিল। জিন্নাহ্ যে ঐল্লামিক রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করেছিলেন (ঘটনাচক্রে তিনি নিজে একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন না) গান্ধিজি ছিলেন তার তীব্র বিরোধী, তিনি সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সমতার পক্ষে ছিলেন। যখন ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসীরা দাবি করেন ধর্ম রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না, তার অর্থ এই নয় যে, একনিষ্ঠ হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান অথবা অন্য যেকোনো ধর্মের অনুসরণকারী কেউ ধর্মসহ সকল সীমার ঊর্ধ্বে উঠে জাতি ও মানবতার জন্য কাজ করবে না।
ধর্ম রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না বলার অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যক্তি যিনি কোনও একটা ধর্মে বিশ্বাস করেন অথবা তাঁদের ধর্মীয় নেতারা রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না। এর অর্থ এই যে, ধর্মীয় নেতাদের যে কর্তৃত্বতা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল বা গ্রুপের পক্ষে বা বিপক্ষে ব্যবহার করা যাবে না। যেসব একনিষ্ঠ খ্রিস্টানরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যেসব একনিষ্ঠ মুসলিম ও হিন্দুরা ইন্দিরা গান্ধির স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, ভারতে যে কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠ মানুষ ‘হিন্দুত্ব’ ধারণার তত্ত্ব ও প্রয়োগের মোকাবিলা করছেন, তাঁরা সকলেই এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক মানুষের সঙ্গে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সপক্ষে লড়াই করতে এগিয়ে আসবেন এবং আসা উচিত। কোনও ধর্মীয় নেতা যাতে তাঁর কর্তৃত্ব’কে কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে অপব্যবহার না করতে পারেন।
সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা যে ধর্মের বিরোধী, এই আশংকার কোনও ভিত্তি নেই। ধর্মনিরপেক্ষতা হল সমাজ স্বার্থ বিরোধী উদ্দেশে ধর্মকে অপব্যবহার করার বিরোধী।
ফ্রন্ট লাইন পত্রিকায় ১৯৯৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরাজি নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ: অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
মুক্তিকামী ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে
লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ‘Liberation Theology’ বা ‘মুক্তিকামী ধর্মতত্ত্ব’ নামে এক তত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে-এ হল খ্রিস্টধর্মেরই এক তত্ত্ব যেখানে খ্রিস্টধর্ম বাস্তবের মাটিতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বল হচ্ছে আদর্শে অটুট থেকেও এবং ধর্মপালন করার পাশাপাশি মার্কসবাদী ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার।
এই আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা আজ তাঁদের নিজ নিজ দেশে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য লড়াইয়ের খাতায় নাম লিখিয়েছেন, কেউ কেউ এই বিপ্লবী সংগ্রামে শহিদও হয়েছেন।
ভারতে যাঁরা একনিষ্ঠ খ্রিস্টান তাঁদের মধ্য থেকে এই ধরনের আন্দোলন আজও তৈরি হয়নি। তবে এদেশে যে তা হতে যাচ্ছে তার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কে এ পলসন, যিনি পরবর্তীকালে অ-ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের বিশপ পলোজ মার পলোজ হয়েছে, তিনি তাঁর ডক্টরেটের থিসিসে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে ডক্টরেটের জন্য গবেষণা করেছিলেন এবং ১৯৭৫ সালের অক্টোবরে তাঁর থিসিস জমা দেন। এটি প্রকাশিত হয়নি তবে লেখক এটি আমাকে দিয়েছেন পড়ার জন্য।
তাঁর থিসিসের শিরোনাম “Bonhoefferian Corrective to Karl Marx’s
Critique of Religion” এই থিসিস পড়লেই বোঝা যায় মুক্তিকামী ধর্মতত্ত্ব ভারতে, বিশেষত কেরালায় আসতে চলেছে।
এই থিসিস তিনভাগে বিভক্ত, এর মধ্যে প্রথম ভাগের পাঁচটি পরিচ্ছেদে ধর্ম বিষয়ে ডার্কসের সমালোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় ভাগেরও পাঁচটি পরিচ্ছেদ সেখানে জার্মান জর্মতাত্বিক বনহোয়েফার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে খ্রিস্টানদের
ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ (১৯০৯-১৯৯৮) ভারতের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ও বড়ো মাপের মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। তিনিই ১৯৫৭ সালে এদেশে সর্বপ্রথম কেরালার কমিউনিস্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন, পরে ঐ পদে আসীন হন ১৯৬৭সালেও। ছিলেন সিপিআই (এম)’র সাধারণ সম্পাদক। সারা জীবন তিনি অজস্র নিবন্ধ লিখেছেন, তাঁর লেখা গ্রন্থও আছে বেশ কিছু। এই বইয়ে সংকলিত প্রবন্ধগুলি প্রধানত ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক।
এন বি এ
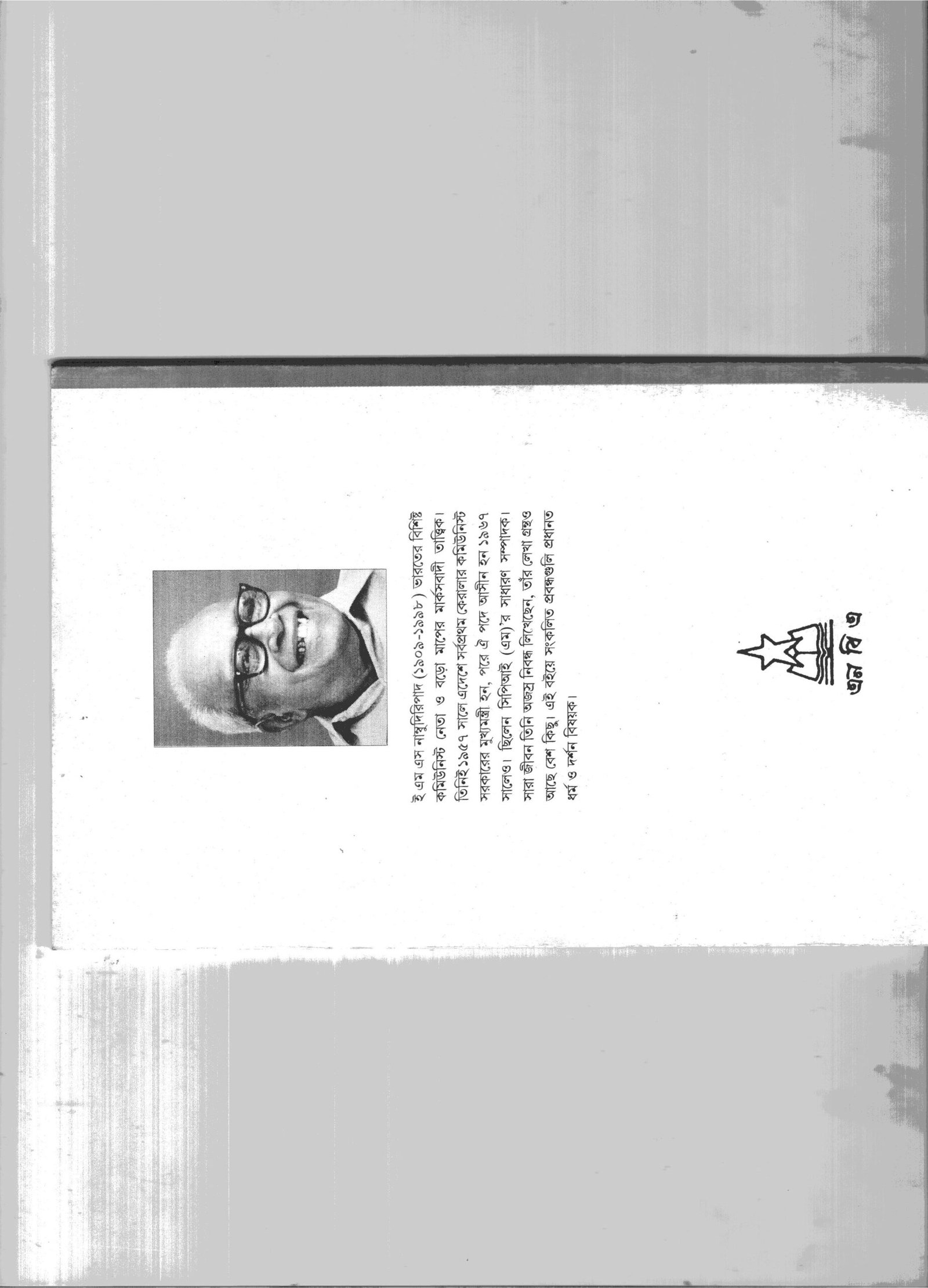
‘জনগণের আফিঙ’: মার্কসিয় তত্ত্ব ও ধর্ম
মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বের যাঁরা প্রবল-সমালোচক অথবা যাঁরা এটির একনিষ্ঠ সমর্থক তাঁরা সকলেই ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের বিখ্যাত ‘ধর্ম হলো জনসাধারণের আফিল্ড’ এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেন এবং তাঁরা সকলেই যেন এবিষয়ে একমত এইটাই ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের মোদ্দা কথা।
তাই মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা যখন জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র, শাস্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রামে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে হাত মেলান তখন অ-মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এই বলে সমালোচনা করেন যে আপনারা ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের সমালোচনাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে নিষ্ঠাবান ধর্মীয় নেতারা মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে বন্দুক তাক করেন এই বলে যে আপনারা “ধর্ম হলো জনগণের আফিপ্ত” এই মন্তব্যটিকে গোঁড়ামি করে আঁকড়ে ধরে বসে আছেন।
কিন্তু উভয়পক্ষই উল্লেখ করতে ভুলে যান যে কোন পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস একথা বলেছিলেন। তিনি “হেগেলের আইন দর্শনের পর্যালোচনায় প্রদত্ত রচনায়” (Contribution to the Critique of Hege’s Philosophy of Right) বলেছিলেন, “মানুষ যে স্বর্গে উদ্ভট বাস্তবতার মধ্যে খুঁজেছি। একটি অতিমানব সত্তা, আর সেখানে সে নিজের প্রতিচ্ছায়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না, সে সেখানে একটা যথার্থতা বাস্তবতা পেতে চায় এবং চাইবেই, সে কেবল নিজ অনুরূপতা, শুধু একটা অ-মানুষ সত্ত্বার সাক্ষাৎ পেতে সে আর বুঝুঁকবেনা।”
তিনি আরো বলছেন, “মানুষ ধর্ম তৈরি করে, ধর্ম মানুষকে তৈরি করেনা। যে মানুষ এখনো নিজেকে খুঁজে পায়না, অথবা হারিয়ে ফেলেছে, ধর্ম সেই আত্মহারা মানুষের আত্মচেতনা এবং আত্মসম্মান। কিন্তু মানুষ তো জগতের বাইরে তাঁবু খাটিয়ে থাকা কোনো বিমূর্ত সত্ত্বা নয়। মানুষ হলো মানব জগতের মানুষ, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার মানুষ। এই রাষ্ট্র, এই সমাজ ধর্মের জন্ম দেয়, ধর্ম একটা ওলটানো জগৎ চেতনা, কারণ রাষ্ট্র ও সমাজটাই একটা ওরুটানো জগৎ। ধর্ম হলো সেই জগতের সাধারণ তত্ত্ব, সর্ববিদ্যার সারাৎসার, সকলে বোঝে এমন যুক্তি, এর আধ্যাত্মিক মর্যাদা, এর উদ্দীপনা, এর নৈতিক অনুমোদন, এর ভাবগম্ভীর সমাপন, এর সান্ত্বনা ও ন্যায্যতা দেওয়ার সর্বব্যাপক ভিত্তিভূমি। এ হলো মানবসত্তার উদ্ভট উপলব্ধি, কারণ মানব সত্ত্বার কোনও প্রকৃত বাস্তবতা নেই। তাই ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হল ধর্ম যে জগতের আধ্যাত্মিক সৌরভ, সেটা বিরুদ্ধে পরোক্ষ লড়াই।” এরপরে তিনি এই বলে শেষ করছেন, “ধর্মীয় যন্ত্রণা হলো একই বাস্তব যন্ত্রণার অভিব্যক্তি এবং বাস্তব যন্ত্রণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। ধর্ম হলো নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, ঠিক যেমন আস্থাবিহীন পরিবেশের আত্মা। ধর্ম হলো জনগণের আফিমও।”
সুতরাং যেসব ধর্মীয় নেতারা মার্কসের সমালোচনা করেন এবং যেসব মার্কসবাদীরা মনে করেন ধর্মকে আফিঙ বলাটা মার্কসের একেবারে সারকথা, তাঁরা উভয়েই পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে এমন কথা বলেন। একথার প্রকৃত অর্থ হলো শ্রেণি শাসনের শোষণে অসহায় মানুষ ধর্মের কাছে কাল্পনিক সাহায্য চায়। ধর্ম সে সাহায্য দেয়, কিন্তু সাময়িকভাবে, ঠিক যেমন কারোর যদি শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হয় তখন আফিল্ড তাকে সাময়িক রিলিফ দেয়। কিন্তু আশু রিলিফ অসুখের প্রকৃত ও স্থায়ী নিরাময়ের বিকল্প নয়। একইভাবে, ধর্ম শোষিত মানুষকে সাময়িক রিলিফ দেয়, স্থায়ী রিলিফ দেয়না। এজন্য মানুষকে নিজেকে সংগঠিত হতে হবে, শ্রেণি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নিয়ে একটি শ্রেণিবিহীন সমাজ গঠন করতে হবে।
এই পরিপ্রেক্ষিতটি যদি সামনে রাখা যায় তবে দেখা যাবে ধর্মের একটা ইতিবাচক উপাদান আছে-তা হলো এটি সাময়িক রিলিফ দেয়-যদিও তা যথেষ্ট’ নয়। প্রকৃত সমাধান হলো শ্রেণি সংগ্রাম। এটাই হলো ধর্ম সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্বের মূল কথা।
এখন দেখা যাক মার্কসের বিখ্যাত সহযোগী ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস তাঁর নিজের লেখা একটি রচনায় এসম্পর্কে কী বলেছিলেন। খ্রিষ্টধর্মের একেবারে গোড়ার যুগের ইতিহাস সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস বিশ্বের দু’টি প্রধান ধর্ম-খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলামের বিকাশকে বোঝার চেষ্টা করেছেন।
“গোড়ার যুগের খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের বেশ কিছু ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের মতোই খ্রিষ্টধর্মও একেবারে শুরুতে শোষিত মানুষের আন্দোলনই ছিল। শুরুতে এটি ক্রীতদাসদের, মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের, সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত গরিব মানুষদের, রোম প্রশাসনের দ্বারা পদানত অথবা বিতাড়িত মানুষজনের ধর্ম হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করে। খ্রিষ্টধর্ম ও শ্রমিকশ্রেণির সমাজতন্ত্র উভয়েই দাসত্ব ও দুর্দশা থেকে আসন্ন মুক্তির কথা বলে।”
এঙ্গেলস আরো লিখছেন “খ্রিষ্টধর্ম ইহজীবনের ওপারে মুক্তির কথা বলে, মৃত্যুর পরে স্বর্গের কথা বলে; অপরদিকে সমাজতন্ত্র এই পৃথিবীতে মুক্তির কথা বলে, সমাজ পরিবর্তনের কথা বলে। উভয়কেই নিগ্রহ করা হয়েছে, বিদ্রূপে জর্জরিত করা হয়েছে, তাদের অনুসরণকারীদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়েছে, তাদেরই মোকাবিলার জন্য তৈরি
আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
হয়েছে আইন, কারণ প্রথম পক্ষটি মানবজাতির শত্রু, দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রের, ধর্মের, পরিবারের ও সামাজিক ব্যবস্থার শত্রু। কিন্তু এত নিগ্রহ করা সত্ত্বেও, ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তারা অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে জয়লাভ করেছে। আবির্ভাবের ৩০০ বছর পর খ্রিষ্টধর্ম রোমান বিশ্বসাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং মাত্র ৬০ বছরে সমাজতন্ত্র যে জায়গায়। এসে পৌঁছেছে তাতে বোঝাই যাচ্ছে এর বিজয়লাভ একেবারে নিশ্চিত।”
এঙ্গেলস একটি পাদটিকায় উল্লেখ করেছেন “এরই একটা অ্যান্টিথিসিস দেখা গেল মুসলিম দুনিয়ার ধর্মীয় উত্থানে, বিশেষ করে আফ্রিকায়। ইসলাম একটি ধর্ম যা প্রাচ্যবাসীদের জন্য তৈরি, বিশেষ করে আরবদের জন্য, অর্থাৎ একদিকে শহরে বাস করা ব্যবসা ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন, অপরদিকে যাযাবর বেদুইনরা। তবে সেখানেও কিছুদিন অন্তর অন্তর সঙ্ঘাতের ভ্রণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। শহরের মানুষ স্বাধীন হয়েছে। বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে, ‘আইন’ মেনে চলার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ঢিলেঢালা ভাব। অপরদিকে বেদুইনরা গরিব কিন্তু কঠোরভাবে নৈতিক। তারা ধনীদের ধনসম্পদ ও আমোদপ্রমোদকে হিংসা করত, ঐগুলির প্রতি লালায়িত হত। এরপর তারা এক পয়গম্বরের অধীনে একত্রিত হলো।”
মার্কস যেখানে সাধারণভাবে ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন সেখানে এঙ্গেলস বিশ্বের দুই প্রধান ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের অনুসন্ধান করেছেন। তবে কি মার্কস, কি এঙ্গেলস কারোর পক্ষে বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ বিষয়ে চর্চা করার মত সময় ও সুযোগ বের করা সম্ভব হয়নি। তাই প্রতিটি দেশে ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে কোনো সামগ্রিক বোঝাপড়া আমরা তাঁদের কাছ থেকে পাইনা।
কিন্তু মার্কস যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে শ্রেণি শাসনের সমাজে মানুষের কষ্ট লাঘবের একটি উপায় হলো ধর্ম, কিন্তু শ্রেণিবিহীন সমাজে ধর্মের প্রয়োজন থাকবে না, অল্প কিছুদিন শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের পর এই শ্রেণিহীন সমাজের আবির্ভাব হবে। বিশ্বের অন্যান। প্রাকৃতিক ও সামাজিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার মতোই ধর্মেরও উদ্ভব, বিকাশ ও পতন আছে। সুতরাং অ-মার্কসবাদী যুক্তিবাদীরা যখন বর্তমান শ্রেণিবিভক্ত সমাজের শ্রেণিসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্মের বিরুদ্ধে বিমূর্ত সংগ্রাম করেন তখন তা বিজ্ঞানসম্মত হয় না। একইভাবে কিছু ধর্মীয় নেতা যখন ভাবেন যে ধর্ম একটি শক্তি হিসাবে অনন্তকাল থেকে যাবে, এমনকি শ্রেণিশোষণ শেষ হলে, শ্রেণিহীন সমাজ গঠিত হলেও থেকে যাবে তখন তাঁরাও একইরকম অবৈজ্ঞানিক চিন্তা করেন।
ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং শ্রেণিসংগ্রামকে সমন্বিত করার বিষয়টিকে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন মার্কস ও এঙ্গেলসের একনিষ্ঠ শিষ্য ভি আই লেনিন তাঁর ‘গ্রামের গরিবদের প্রতি’ পুস্তিকাতে। তিনি লিখছেন, “সোস্যাল ডেমোক্রাটরা আরও দাবি করে প্রতিটি মানুষের তার পছন্দমতো ধর্মপালনের সম্পূর্ণ বাধাহীন অধিকার থাকবে। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে একমাত্র রাশিয়া এবং তুরস্কে লজ্জাজনক আইন রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে অর্থোডক্স ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় উপদলগুলি, সঙ্কীর্ণতাবাদীরা এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এইসব আইনের সাহায্যে কিছু ধর্মকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে অথবা তার প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অথবা এর অনুগামীদের কিছু অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এইসব আইন সম্পূর্ণত অন্যায়, স্বৈরাচারী এবং লজ্জাজনক।” এরপরে তিনি উল্লেখ করছেন একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ কীভাবে ধর্মকে মোকাবিলা করবে। তিনি লিখছেন, প্রত্যেকে অবশ্যই তার পছন্দমতো ধর্মে বিশ্বাস করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে অথবা নিজের ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবে। কারোর ধর্মসম্পর্কিত বিষয়ে কোনও কর্তাব্যক্তির কোনও প্রশ্ন করারও অধিকার থাকবে না; এ হলো প্রতিটি মানুষের বিবেকের প্রশ্ন এবং কারোর সেখানে হস্তক্ষেপের কোনোরকম অধিকার নেই। কোনো সরকারি ধর্ম অথবা সরকারি চার্চ থাকবে না। আইনের দৃষ্টিতে সকল ধর্ম এবং চার্চ সমান বলে গণ্য হবে। প্রত্যেক ধর্মের যাজকদের বেতন তাদের ধর্মীয় সংগঠন থেকেই দিতে হবে, রাষ্ট্র তার অর্থ দিয়ে কোনো ধর্মকে সমর্থন করবে না এবং কোনো যাজকের বেতনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে না, তা সে অর্থোডক্স, বিভিন্ন ধর্মীয় উপদল, সঙ্কীর্ণতাবাদী অথবা যাই হোক না কেন। এরজন্যই সোস্যাল ডেমোক্রাটরা লড়াই চালাচ্ছে। কোনোরকম ওজর আপত্তি এবং পাশ কাটানো ছাড়া যতদিন এইসব পদক্ষেপগুলি কার্যকর করা না হচ্ছে, ততদিন ধর্মের উপর লজ্জাজনক পুলিশী নির্যাতন থেকে এবং এইসব ধর্মের বিরুদ্ধে পুলিশের থেকে প্রচার করা পুস্তিকাগুলি যা আরও বেশি লজ্জাজনক, তা থেকে মানুষকে মুক্ত করা যাবেনা।”
উপরোক্ত মন্তব্যগুলি থেকে বোঝা যায় যে, এগুলি হলো উনিশ শতকের বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের আদর্শ যা গ্রহণ করা হয়েছিল আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজন অনুসারে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ধর্ম সম্পর্কে একটি শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের অবস্থান কী? এবিষয়ে লেনিন তাঁর আরেকটি নিবন্ধ-‘সমাজতন্ত্র ও ধর্ম’তে উত্তর দিয়েছেন। তিনি তিনটি প্রধান পর্যবেক্ষণ এখানে উপস্থিত করেছেন।
প্রথমত “ধর্মকে অবশ্যই ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার বলে ঘোষণা করা উচিত। এ উক্তিতে সাধারণত ধর্ম সম্পর্কে সমাজতন্ত্রীদের মনোভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোনোরকম বিভ্রান্তির সম্ভাবনা এড়িয়ে চলার জন্য এইসব শব্দাবলির অর্থ সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়া দরকার। রাষ্ট্রের নিরিখেই আমরা দাবি করছি যে ধর্ম হলো একটি ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু তার অর্থ কখনই এটা নয় যে, আমাদের পার্টির অভ্যন্তরেও আমরা ধর্মকে একটি ব্যক্তিগত বিষয় বলে মনে করি। ধর্ম নিয়ে রাষ্ট্রের কোনো গরজ থাকবে না এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাগুলি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে না।”
“কিন্তু একটি সমাজতন্ত্রী প্রলেতারীয় পার্টির পক্ষে ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিষয় নয়। আমাদের পার্টি হলো শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির জন্য আগুয়ান যোদ্ধাদের সমিতি। এইরকম একট সমিতি ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শ্রেণিচেতনার অভাব, অজ্ঞতা এবং সত্যানুসন্ধানবিরোধী মানসিকতা সম্পর্কে নির্বিকার থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়। আমরা চাই রাষ্ট্রের সঙ্গে গির্জার সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ যাতে আমরা আমাদের নিখাদ মতাদর্শ এবং একমাত্র মতাদর্শগত অস্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ আমাদের প্রকাশনা এবং মৌখিক প্রচারের মাধ্যমে ধর্মীয় কুয়াশার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি।”
আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
দ্বিতীয়ত “আমরা কেন আমাদের কর্মসূচিতে নিজেদের নাস্তিক বলে ঘোষণা করছি। না?” এই প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন লেনিন। তিনি ব্যাখ্যা করছেন “আমাদের কর্মসূচি সম্পূর্ণত বৈজ্ঞানিক এবং সেইসঙ্গে বস্তুবাদী, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। সুতরাং যেখানে আমাদের কর্মসূচি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, সেখানে এই ব্যাখ্যাও দিতে হবে যে, এই ধর্মীয় কুয়াশার প্রকৃত ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক শিকড় কোথায় নিহিত। আমাদের প্রচারে নাস্তিক্যবাদের প্রচারও প্রয়োজন; যথাযথ বৈজ্ঞানিক বইপত্র প্রকাশ করতে হবে যা এতদিন স্বৈরাচারী সামন্ততান্ত্রিক সরকার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং হেনস্থা করেছে-এগুলিই এখন পার্টির অন্যতম কর্মক্ষেত্রে হওয়া উচিত। … কিন্তু কোনো অবস্থাতে আমরা ধর্মীয় প্রশ্নটিকে বিমূর্ত, আদর্শগত কায়দায় এবং শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন বৌদ্ধিক প্রশ্ন হিসাবে বিচার করবো না, যা বুর্জোয়াদের মধ্যে র্যা ডিক্যাল ডেমোক্রাটরা প্রায়ই করে থাকেন। যে সমাজে অন্তহীন শোষণ চলছে এবং শ্রমিকশ্রেণিকে অমার্জিত করে তোলা হয়, সেখানে কেবলমাত্র প্রচার দিয়ে ধর্মীয় কুসংস্কারকে দূর করা যাবে একথা ভাবা নির্বুদ্ধিতা হবে। মানুষের ওপর চেপে থাকা ধর্মের জোয়াল যে সমাজের মধ্যে থাকা অর্থনৈতিক জোয়ালের প্রতিফলন ও ফল-এইটা বিস্মৃত হওয়া বুর্জোয়া সংকীর্ণতারই শামিল। পুঁজিবাদের তমসাচ্ছন্ন শক্তির বিরুদ্ধে নিজে সংগ্রামে যুক্ত থেকে যে সর্বহারা নিজে আলোকপ্রাপ্ত হয়নি তাকে যতই প্রচারপুস্তিকা দেওয়া হোক না কেন এবং যতই প্রচার করা হোক না কেন, সে আলোকপ্রাপ্ত হবে না। পরলোকে স্বর্গসৃষ্টির জন্য সর্বহারার জনমতকে ঐক্যবদ্ধ করার চেয়ে এই পৃথিবীর বুকে স্বর্গ তৈরির জন্য শোষিত শ্রেণিগুলির প্রকৃত বিপ্লবী সংগ্রামের ঐক্য গড়ে তোলা অনেক বেশি জরুরী।” (গুরুত্ব আরোপ এই লেখকের)
তৃতীয়ত “একারণেই আমাদের কর্মসূচিতে আমরা আমাদের নাস্তিক্যবাদ ঘোষণা করিনি, করা উচিতও নয়। একারণেই যেসব সর্বহারা আজও অতীত কুসংস্কারের কোনো না কোনো জের বজায় রেখেছে তাদের পক্ষে আমাদের পার্টির কাছাকাছি আসা নিষিদ্ধ করা হয়নি, করা উচিতও নয়। আমরা সবসময়ই বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা প্রচার করবো, নানা ধরনের খ্রিশ্চানদের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা একান্ত প্রয়োজন। এর অর্থ এই নয় যে ধর্মের প্রশ্নকে আমাদের সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া উচিত, যা তার আদৌ প্রাপ্য নয়; এর অর্থ এটাও নয়, যে আমরা সত্যিকারের বিপ্লবী, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে তৃতীয় শ্রেণির মতামত ও বোধবুদ্ধিহীন ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ভেঙে টুকরো করবো। এইসব ধ্যানধারণা দ্রুত তার রাজনৈতিক গুরুত্ব হারাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক বিকাশের ধারায় তা আবর্জনার মতো দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। (গুরুত্ব আরোপ এই লেখকের)
ধর্ম ও শ্রেণিসংগ্রামের মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের লেখা থেকে যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি উপস্থিত করা হলো তা থেকে যা বেরিয়ে আসছে-
১। অমার্কসীয় যুক্তিবাদীরা যেভাবে শ্রেণিসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিমূর্ত ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, আমরা সেভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করব না।
‘জনগণের আফিন্দ্র’: মার্কসিয় তত্ত্ব ও ধর্ম
২। গণতান্ত্রিক এবং সর্বহারার আন্দোলনে যে পশ্চাদপদ অংশ আছে, যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অথচ যাদের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কারের রেশ রয়ে গেছে তাদেরকে এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রেণিসংগ্রামের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করতে হবে এবং মার্কসবাদী লেনিনবাদী দর্শন অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাই জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় ঐকা, বিশ্বশান্তি এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা
করবো, তেমন আমাদের অবশ্যই ধর্মীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে যে
মতাদর্শের প্রতি আমাদের অনেক বন্ধু আজও দায়বদ্ধ।
দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের জন্য আমরা আমাদের দৃড় সঙ্কল্পবদ্ধ সংগ্রামকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারি না। কিন্তু একইসঙ্গে অভিন্ন সংগ্রামে বিভিন্ন ধর্মীয় মানসিকতাসম্পন্ন জনসাধারণ ও তাদের নেতাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে যেতে হবে।
ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় ১৮ই নভেম্বর, ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ: অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
রাজনীতি ও সমাজজীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায়?
মধ্যে সহযোগিতার ধারণকে প্রসারিত করতে তিনি বড় অবদান রেখেছেন। ধর্মকে যাঁরা মানেন এবং যাঁরা মানেন না তাঁদের পরস্পরের মধ্যে আলোচনা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। উভয়পক্ষ একমত হতে পারেন এমন বিষয়ই আলোচনায় আসতে পারে।
রাজনীতি ও সমাজজীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায়?
সম্প্রতি “ধর্মনিরপেক্ষতার অভিমুখে কেরালা” শীর্ষক এক সেমিনারের উদ্বোধন করে, কেরালার খ্রিশ্চান অর্থোডক্স চার্চের অত্যন্ত সম্মানীয় নেতা ড. পলোজ মার গ্রেগরিয়স বলেছেন, “যদিও আমি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষজন এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে সাধারণভাবে একমত, তবে আমি মনে করি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভবও নয়, উচিত নয়।”
তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, সমাজ এবং সংস্কৃতিকে ধর্মের থেকে আলাদা করা যায় না: অপরদিকে ধর্মের থেকে রাজনীতিকে আলাদা করা সম্ভব এবং প্রয়োজন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের কোনো নিজস্ব ধর্ম থাকবে না, একজন ব্যক্তি তিনি পুরুষ অথবা নারী যাই হোন না কেন তাঁর ইচ্ছামতো ধর্মবিশ্বাস পোষণ করবেন, পালন করবেন এবং প্রচার করবেন। তিনি আরো বলেন মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিচালনা করে তার ধর্ম, তাই একটা দেশের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনকে গড়ে তুলতে ধর্মকে একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।
ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব ও বিকাশকে খুঁজতে গিয়ে মারগ্রেগরিয়স বলেন, ইউরোপে আলোকপ্রাপ্তি ও রেঁনেসার সময় ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হয়। এই ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল নাস্তিকতার আদর্শে চালিত যেখানে ঈশ্বর ও ঈশ্বর-নির্ভর ধর্মকে অস্বীকার করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, একজন সক্রিয় খ্রিস্টান হিসাবে এই ধরনের ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষতাকে (নাস্তিকতার ঝোঁকসহ) কেরালার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে আমদানি করতে তিনি দেবেন না।
এর অর্থ এই নয় যে, তিনি অধার্মিক ও নাস্তিকদের প্রতি অসহিষ্ণু। প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর যে বোঝাপড়া বিশেষ করে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে, তার সঙ্গে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতা ও কমিনিউজমের ধারণায় অনেকটাই ঐকমত্য রয়েছে।
শুধু ভারতেই নয়, বিদেশেও তিনি “কমিউনিস্টদের সহযাত্রী” হিসাবেই পরিচিত। বাস্তব জীবনে একদিকে ধর্মীয় নেতা এবং অপরদিকে ধর্ম মানে না এমন নাস্তিক কমিউনিস্টদের
মার গ্রেগরিয়াসের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে যে ইতিবাচক উপাদান আছে তাকে স্বীকার করার পর একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর পক্ষে তাঁর এই যুক্তির বিরুদ্ধে পালটা উত্তর দিতেই হবে, যেখানে তিনি বলছেন মানবতা ও নৈতিকতার জন্য ধর্মের নেতৃত্ব প্রয়োজন। মার গ্রেগরিয়সের বক্তব্য এই যে, সাধারণভাবে নাস্তিকতার এবং বিশেষ করে কমিউনিজম ধর্মবিরোধী এই অর্থে যে তারা দৈনন্দিন কাজের জগতে ধর্মবিশ্বাসী ও আধ্যাত্মিক নেতাদের আক্রমণ করে থাকেন।
এক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের একথা বলতে হবে যে তিনি সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা একমাত্র সত্য অ-মার্কসবাদী যুক্তিবাদীদের ক্ষেত্রে যাদের কাছে ধর্ম ও ঈশ্বরের বিরোধিতাই হল মতাদর্শগত সংগ্রামের শুরু এবং শেষ। তাঁর মতো ধর্মীয় নেতা, ধর্ম মানেন না এমন মানুষ এবং নাস্তিক কমিউনিস্টদের মধ্যে আলোচনা ও সহযোগিতার ভাবনাকে বর্তমান সময়ের কমিউনিস্টরাও সমর্থন করে।
এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা দরকার কেন সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে আলোকপ্রাপ্তি ও রেঁনেসার সাধারণ অভিমুখ ছিল ধর্মের বিরুদ্ধে। সামন্ত সমাজের অন্ধ ধর্মীয় মতাদর্শে মধ্যযুগের ইউরোপ তলিয়ে গিয়েছিল। ইনকুইজিশনের (ধর্মদ্রোহিদের দমন করার জন্য রোমান ক্যাথলিক চার্চ দ্বারা নিযুক্ত আদালত-অনুবাদক)
মত কার্যকলাপের দ্বারা খ্রিস্টান চার্চ ও তাদের নেতাদের ব্যবহার করা হত সাধারণ মানুষের উপর সামন্তপ্রভু ও রাজাদের আধিপত্যকে বজায় রাখতে।
যখন আধুনিক গণতান্ত্রিক ধারণার ঝড় বয়ে গেল মধ্যযুগের ইউরোপে, তখন আলোকপ্রাপ্ত মানুষেরা ধর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, যা ছিল সে সময়ে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পূর্বশর্ত।
যেমন মার্কস বলেছেন, “সমালোচনা শুরুই হচ্ছে ধর্মের সমালোচনা দিয়ে।” যদি সেদিন সামন্তপ্রভুদের সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের অবসান ঘটাতে হত, তাহলে মধ্যযুগের ইউরোপীয় চার্চের ইনকুইজিশন ও অন্যান্য বর্বরোচিত প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত করতেই হতই।
এই পটভূমিতেই অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে ধর্মের থেকে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ আলাদা করার দাবি ওঠে। আলোকপ্রাপ্ত মানুষেরা যে সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার এই তিনটি স্লোগান উত্থাপন করেছিলেন, তা যদি বাস্তবে প্রয়োগ করতে হত, তবে মধ্যযুগীয় চার্চ নেতাদের
শক্তিশালী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হত। ভারতেও উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক নবজাগরণের উত্থানের ফলে জন্ম হয় (জ-মার্কসবাদী) ‘যুক্তিবাদ’-এর। এই প্রবণতার যাঁরা প্রবক্তা তাঁদের মতে মার্কসের কথামতো ধর্ম দিয়ে শুধু সাধারণ সমালোচনার সূত্রপাতই হচ্ছে না সমালোচনার শেষও
আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
হবে ধর্মকে দিয়ে। মার্কসবাদীরা যে ধর্ম ও ঈশ্বরের সমালোচনা করে তা হল তাদের ভূস্বামী-বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনেরই একটা অংশ, কিন্তু অ-মার্কসবাদী যুক্তিবাদীরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে ধর্মের বিরুদ্ধে, কেবলমাত্র ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেই। অপরদিকে মার্কসবাদীরা মনে করে যে শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শ ও তার প্রয়োগের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা যে লড়াই করছে, তাতে তাদের অস্ত্রাগারে মতাদর্শগত অস্ত্র হল ধর্ম। ভূস্বামী পুঁজিপতি শ্রেণির হাত থেকে যদি মানবতাকে সামগ্রিক মুক্তি এনে দিতে হয় তবে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ধর্ম মানেন এবং ধর্ম মানেন না এমন সংগ্রামী মানুষের ঐক্য প্রয়োজন, এটা মতাদর্শ হিসাবেই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে।
মার্কসবাদী নিঃসন্দেহে মতাদর্শ মনে করেই ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করে, কারণ ধর্ম তাদের শ্রেণিসংগ্রামের সংগ্রামী জনতাকে দিকভ্রান্ত করে দেয়। অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ধর্ম-বিশ্বাসী ও ধর্মে অবিশ্বাসী উভয়েরই যে অভিন্ন লড়াই সেখানে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ না করে ধর্ম জনসাধারণকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে এই জগতে পুঁজিপতি-ভূস্বামীশাসিত সমাজের অসুবিধাগুলি সহ্য কর, তাহলে তোমরা ‘অন্য দুনিয়া’-র ‘স্বর্গে’ পৌঁছাতে পারবে। তাই মার্কসবাদীরা মনে করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শ যার ভিত্তি হল বস্তুবাদী দর্শন, তা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া তার পবিত্র কর্তব্য। তাই পার্টির সকল সদস্য, যাঁরা পার্টিকে শক্তিশালী করার কাজ করতে প্রস্তুত, তাঁরা তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বস্তুবাদের প্রচারে, সাধারণ বস্তুবাদ নয়, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রচারে। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদেই মার্কস ঘোষণা করেছেন “দর্শন তার বস্তুগত
অস্ত্র পায় শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে এবং শ্রমিকশ্রেণি এই দর্শনে পায় তার আত্মিক অস্ত্র।” তাই শ্রমজীবী মানুষকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আদর্শে শিক্ষিত করে তোলা হল প্রত্যেক পার্টি সদস্যের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং যাঁরা পার্টির সদস্য হতে চান তাঁদেরও এ কাজ করতে হবে।
তবে মার্কসবাদীরা একথা জানেন যে যাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চেতনাকে আয়ত্ত করেছেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের চেতনা যাঁদের হয়েছে তাঁরা প্রতিটি দেশেরই জনসাধারণের এক ক্ষুদ্র অংশ। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সমাজের ক্ষুদ্র অংশ এটা ভাল করে বুঝেই তাদেরকে বিপুল অংশের মানুষকে সঙ্গে নিতে হবে, যে মানুষ কোনো না কোনো ধর্ম বিশ্বাস করে, পালন করে, প্রচার করে। এই দৃষ্টিকোণ যেখানে ধর্মে বিশ্বাসী ও ধর্মে অবিশ্বাসীদের মধ্যে আলোচনা ও সহযোগিতার কথাটা আসছে।
সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, মার গ্রেগরিয়সের মতো ধর্মীয় নেতারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ প্রচারের স্বার্থেই ধর্মবিশ্বাসী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে আলোচনা ও সহযোগিতা প্রয়োজন, অপরদিকে মার্কসবাদীরা মনে করে বর্তমান সমাজের যা কিছু পচা তার বিরুদ্ধে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের অভিন্ন সংগ্রামের ঐক্য গড়ে তোলা দরকার এবং ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে এগোনো দরকার। তাঁরা এটা আশা করেন না যে ধর্মীয় নেতারা তাঁদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মপালন ছেড়ে দেবেন। তাঁরা নিজেরাও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ভিত্তিক মতাদর্শকে ছেড়ে দিতে রাজি নন।
রাজনীতি ও সমাজজীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায়?
সুতরাং ধর্মে বিশ্বাসী এবং মার্কসবাদীদের মধ্যে যদি আলোচনা ও সহযোগিতা গড়ে তুলতে হয় তবে উভয় পক্ষকেই বুঝতে হবে যে অপরপক্ষ কোথায় অবস্থান করছে, যদি কেউ নিজেদের মতাদর্শগত অবস্থানকে ছেড়ে না দিয়েও বাস্তব জীবনের ও সংগ্রামে পরস্পর সহযোগিতা করতে পারে।
সুতরাং একথার কোনও ভিত্তি নেই যে তথ্যগতভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্মবিরোধী আন্দোলন, যেমনটা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলোকপ্রাপ্তদের মধ্যে অথবা আজকের দিনে ভারতে অ-মার্কসবাদী যুক্তিবাদীরা যা করে থাকেন। মার গ্রেগরিয়সের মতো প্রবল ধর্মবিশ্বাসীরাও কমিউনিস্টদের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে স্থান পেতে পারেন। ধর্মবিশ্বাসী ও নাস্তিক উভয়কেই শুধু একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, অভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উভয়পক্ষকে অপরের বিশ্বাস ও কার্যকলাপকে সহ্য ও সম্মান করতে হবে। এটাই হল একমাত্র শর্ত যার ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক (সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক) আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব।
এই বিষয়টি স্পষ্ট করার পর মার গ্রেগরিয়সের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে যেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি হল ধর্ম। একজন প্রবল কমিউনিস্ট বিরোধীও স্বীকার করবেন যে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও তাঁর অনুগামীরাও উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন রাজনৈতিক মূল্যবোধের মানুষ ছিলেন। তাঁরা তাঁদের জীবনে লড়াই করতে গিয়ে বহু যন্ত্রণা ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাঁরা এই কষ্ট সহ্য করেছিলেন কারণ তাঁরা একটা আদর্শের কাছে দায়বদ্ধ থেকে কাজে নেমেছিলেন এবং লড়াই করেছিলেন।
এই উচ্চনৈতিক মূল্যবোধের উদ্ভব হয়েছে তাঁদের সেই মতাদর্শ অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ থেকে। বিপ্লবের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, ‘অন্য জগৎ’-এর পরিবর্তে এই পৃথিবীর মাটিতেই স্বর্গ রচনার সংকল্প, এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মানবতাবাদ। ধর্মীয় নেতাদের প্রতি তাঁদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা জানিয়েও একথা বলা যেতে পারে মানুষের সেবায় নিজেকে নিবেদনের ক্ষেত্রে তাঁরা কেউই মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের সমকক্ষ নন এবং যে সেবাকেই ‘ঈশ্বর’-কে সেবা বলে বর্ণনায় এসেছেন শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নেতারা।
তাহলে প্রশ্ন হল আমরা কেন শুধু রাজনীতিতে নয়, সামাজিক রাজনৈতিক জীবনেও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছি। এর উত্তর হল ধর্মনিরপেক্ষতা হল সকল ধর্মের প্রতি এবং নাস্তিকতার প্রতিও সমান শ্রদ্ধা। যদি এইভাবে সকল ধর্ম ও নাস্তিকতার প্রতি সমমর্যাদার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সহনশীলতা তৈরি হবে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর পছন্দ অনুযায়ী ধর্মবিশ্বাস, পালন ও প্রচার করতে পারবেন অথবা কেউ ইচ্ছা করলে কোনো ধর্মের প্রতি বিশ্বাস না রেখেও বলতে পারবেন। এই ধরনের সমমর্যাদা ও সহনশীলতাই একটা পরিশীলিত সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
ফ্রন্টলাইন পত্রিকার ২ ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরেজি নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ: অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
ধর্মনিরপেক্ষতা কী ধর্মবিরোধী?
ধর্মনিরপেক্ষতা কী ধর্মবিরোধী?
ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে এক বিতর্কে কেরালার অর্থোডক্স খ্রিস্টান চার্চের সম্মানীয় নেতা পওলোজ মার গেগোরিয়স স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে অস্বীকার করে। একজন একনিষ্ঠ খ্রিস্টান হিসাবে তিনি সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করার কথা ভাবতে পারেন না।
তবে তিনি একথাও বলেছেন, তিনি ধর্মকে রাষ্ট্রের মদত দেওয়া অথবা কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র অবস্থান নিক-এটাও তিনি চান না। তাঁর দর্শনের ভিত্তি হল, সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা। তাই আরও এক কদম এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের উচিত নয় কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভরতুকি দেওয়া অথবা মদত জোগানো।
ধর্মপ্রাণ মানুষকে তাদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের মতো করে কাজ করতে দিতে হবে। তাঁর নিজের চার্চ ও অন্যান্য চার্চগুলির অধীনে এবং অখ্রিস্টান অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণে থাকা মানুষজনকে কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে ব্যবহার করার তিনি বিরোধী।
এক্ষেত্রে যখন প্রশ্ন ওঠে, তাঁর এই অবস্থান কী ধর্মনিরপেক্ষ নয়? তার জবাবে তিনি বলেন, না, নয়। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্মকে অস্বীকার করা।
কেরালার অর্থোডক্স চার্চের সম্মানীয় নেতার এই মূল্যায়ন ভারতীয় সংবিধানেরও বিরোধী, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার এই উদাহরণকে তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যখন কোনো সাংসদ, বিধায়ক বা মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন, তখন ভারতীয় সংবিধানে ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের জন্য ‘ঈশ্বরের নামে শপথ’ নেওয়ার এবং ধর্ম বিশ্বাস করেন না-এমন মানুষের জন্য সংবিধানের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে “গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে শপথ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে এই রীতির মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ী এবং ধর্ম মানে না-এমন মানুষ-সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
বেশিরভাগ বিধায়ক, সাংসদ এবং মন্ত্রীরা ঈশ্বরের নামে শপথ নেন এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ ‘গভীর আন্তরিকতা’র সঙ্গে শপথ গ্রহণ করেন। এখানে ধর্মকে অস্বীকার করার কোনও ব্যাপার নেই, বরং ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং ধর্ম মানেন না, এমন মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা রক্ষা করা হয়েছে।
মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাঁদের দিক থেকে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাঁরা যেকোনো ধর্মকে রাজনৈতিক কাজে (নির্বাচন ও অন্যত্র) ব্যবহার করার বিরোধী, কিন্তু তাঁরা জনসাধারণের ধর্মীয় ভাবাবেগকে সম্মান করেন এবং তাঁরা এমন কিছু করবেন না, যা তাঁদের ভাবাবেগে আঘাত করে। তাঁরা তাঁদের ধর্ম না মানার অধিকারকে যেমন দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন, তেমনি ধর্মীয় মানুষজনের নিজস্ব ধর্মে বিশ্বাস ও পালনের অধিকারকে সম্মান। করেন। ঘুরিয়ে বলতে গেলে তাঁরা ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে তাঁদের নিজ ক্ষেত্রে যা প্রাপ্য, তা দেওয়ার পক্ষপাতী “ঈশ্বরকে যা দেওয়ার তা ঈশ্বরকে দাও, রাষ্ট্রকে যা দেওয়ার, তা রাষ্ট্রকে।” ধর্মনিরপেক্ষতার এই বাকা এবং আদর্শকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বিশ্বাস করে।
যদিও আরও কিছুটা এগিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদীরা শোষক শ্রেণি যে ‘ধর্ম’কে বিশ্বাস করে এবং পালন করে, তার বিরুদ্ধে প্রকৃত ধর্মের যা কিছু ইতিবাচক খুঁজে বের করে। মধ্যযুগে ইউরোপ এবং এশিয়াতে যে ধর্মীয় রাষ্ট্র ছিল, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তার বিরোধী। এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিকাশমান পুঁজিবাদ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত করেছিল। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে এই উত্তরণের পথে ধর্মের বিরুদ্ধেই ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল।
যাঁরা এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা ধর্মকেই আক্রমণ করেছিলেন, সামন্ত্রতন্ত্র-বুর্জোয়া শাসকশ্রেণিকে তাদের নিজস্ব স্বার্থে ধর্মকে অপব্যবহার করতে দেয়নি। এই ছিল ইউরোপের বুর্জোয়া ধর্মনিরপেক্ষতার চেহারা, যার সঙ্গে সম্মানীয় খ্রিস্টান নেতা পরিচিত। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলসের এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না,
ছিল না লেনিন ও ফিদেল কাস্ত্রোসহ অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদেরও। মার্কস তাঁর এক বিখ্যাত রচনায় বলেছেন যে, সাধারণভাবে সমাজের সমালোচনার সূচনাই হচ্ছে ধর্মের সমালোচনা দিয়ে।
একদম গোড়ার যুগের খ্রিস্টধর্মের আদর্শ সম্পর্কে খুবই প্রশংসা করেছেন এঙ্গেলস এবং তিনি বলেছেন, আজকের দিনের আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের দলিলের মধ্যে সেই আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাবে।
লেনিন তাঁর দিক থেকে সমস্ত ধর্মীয় ও ধর্মে অবিশ্বাসী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছিলেন, ‘অন্য পৃথিবীতে স্বর্গ আছে কি নেই-এই নিয়ে অনুমান না করে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনার’ জন্য।
ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন, কীভাবে শৈশবে ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম তাঁকে একজন আধুনিক গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ এবং শ্রমিকশ্রেণির যোদ্ধা হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।
আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
সুতরাং এখানে আলোচ্য বিষয় হল, মূল ধর্মগুরুরা ধর্ম নিয়ে কী ভেবেছিলেন এবং পরবর্তীকালের শোষকশ্রেণির প্রজন্ম কীভাবে ধর্মকে ব্যবহার করেছে সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রাখতে ও অত্যাচার চালাতে।
লক্ষ্যণীয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ সময়ে যিনি ছিলেন সর্বোচ্চ নেতা, সেই মহাত্মা গান্ধি ভারতের গরিব মানুষকে ‘দরিত্র নারায়ণ’ বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক গভীর ধর্মবিশ্বাসী মানুষ এবং এদেশের শ্রমিক ও কৃষকদের জীবন্ত দেবতা বলেই গণ্য করতেন এবং তাদের সেবায় জীবনভর পরিশ্রম করে গেছেন।
একজন হিন্দু মতান্ধ ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করেছিল, কারণ একনিষ্ঠ হিন্দু হয়েও মুসলিমদের প্রতি ‘গান্ধিজির সমান শ্রদ্ধা ছিল। জিন্নাহ যে ঐস্লামিক রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করেছিলেন (ঘটনাচক্রে তিনি নিজে একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন না) গান্ধিজি ছিলেন তার তীব্র বিরোধী, তিনি সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সমতার পক্ষে ছিলেন। যখন ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসীরা দাবি করেন ধর্ম রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না, তার অর্থ এই নয় যে, একনিষ্ঠ হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান অথবা অন্য যেকোনো ধর্মের অনুসরণকারী কেউ ধর্মসহ সকল সীমার ঊর্ধ্বে উঠে জাতি ও মানবতার জন্য কাজ করবে না।
ধর্ম রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না বলার অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যক্তি যিনি কোনও একটা ধর্মে বিশ্বাস করেন অথবা তাঁদের ধর্মীয় নেতারা রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না। এর অর্থ এই যে, ধর্মীয় নেতাদের যে কর্তৃত্বতা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল বা গ্রুপের পক্ষে বা বিপক্ষে ব্যবহার করা যাবে না। যেসব একনিষ্ঠ খ্রিস্টানরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যেসব একনিষ্ঠ মুসলিম ও হিন্দুরা ইন্দিরা গান্ধির স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, ভারতে যে কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠ মানুষ ‘হিন্দুত্ব’ ধারণার তত্ত্ব ও প্রয়োগের মোকাবিলা করছেন, তাঁরা সকলেই এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক মানুষের সঙ্গে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সপক্ষে লড়াই করতে এগিয়ে আসবেন এবং আসা উচিত। কোনও ধর্মীয় নেতা যাতে তাঁর কর্তৃত্বকে কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে অপব্যবহার না করতে পারেন।
সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা যে ধর্মের বিরোধী, এই আশংকার কোনও ভিত্তি নেই। ধর্মনিরপেক্ষতা হল সমাজ স্বার্থ বিরোধী উদ্দেশে ধর্মকে অপব্যবহার করার বিরোধী।
ফ্রন্ট লাইন পত্রিকায় ১৯৯৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরাজি নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ: অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী





